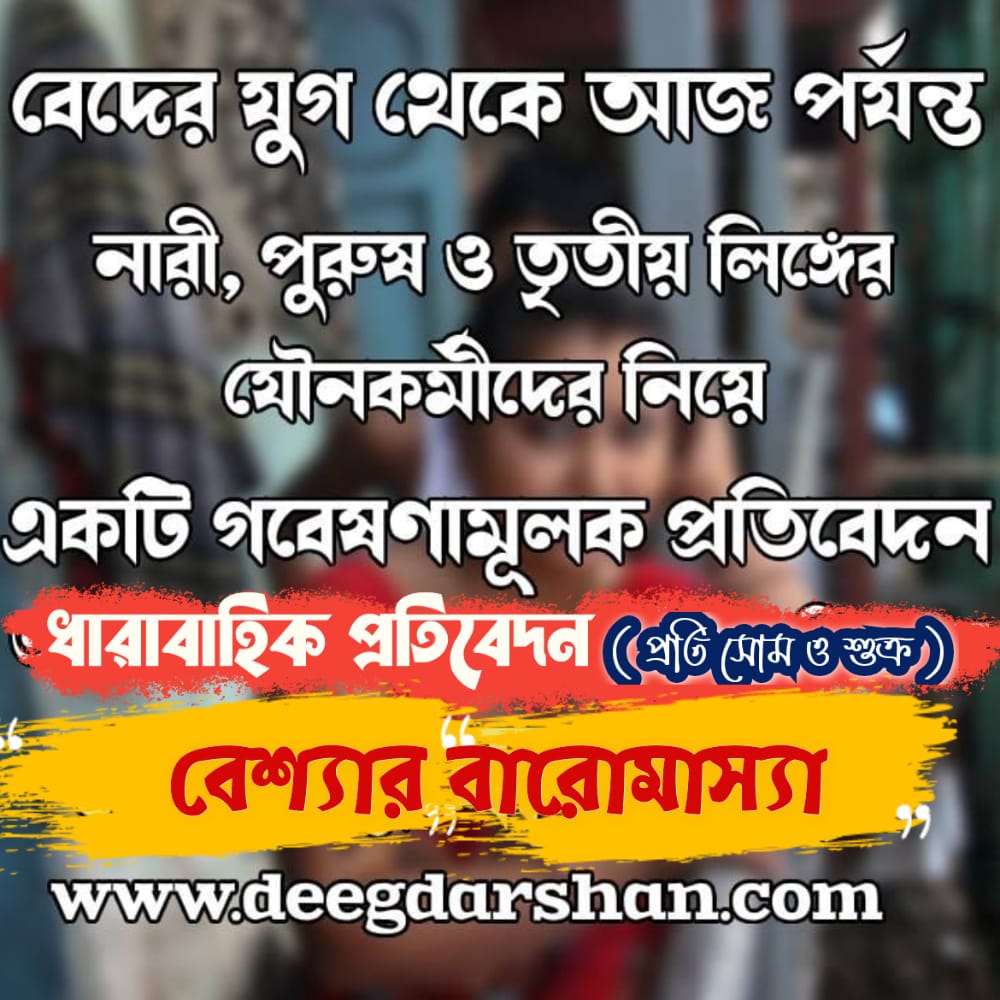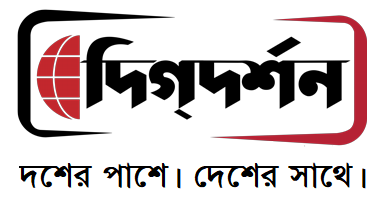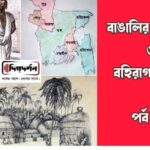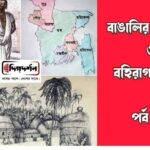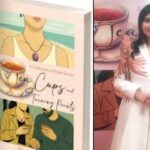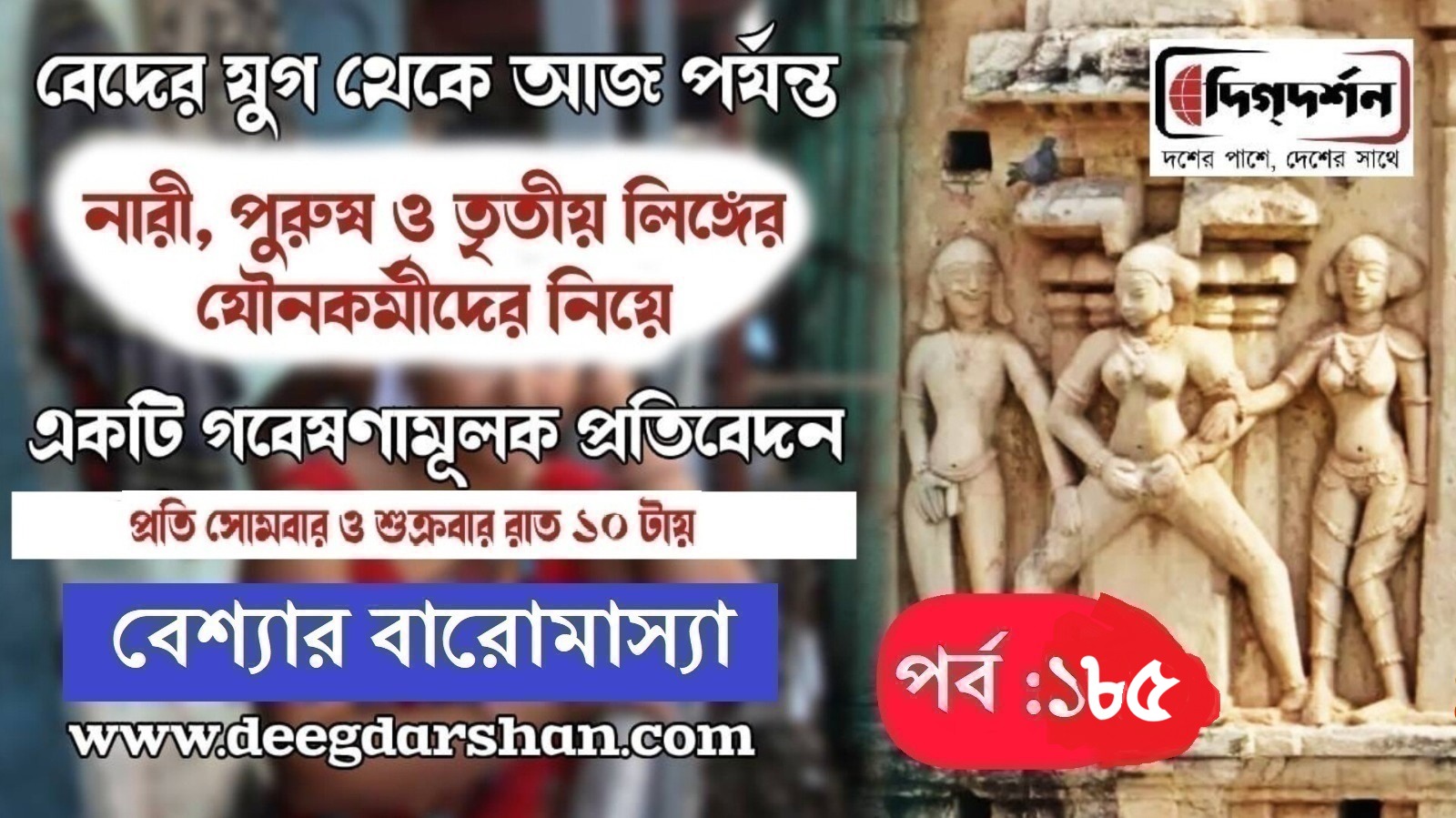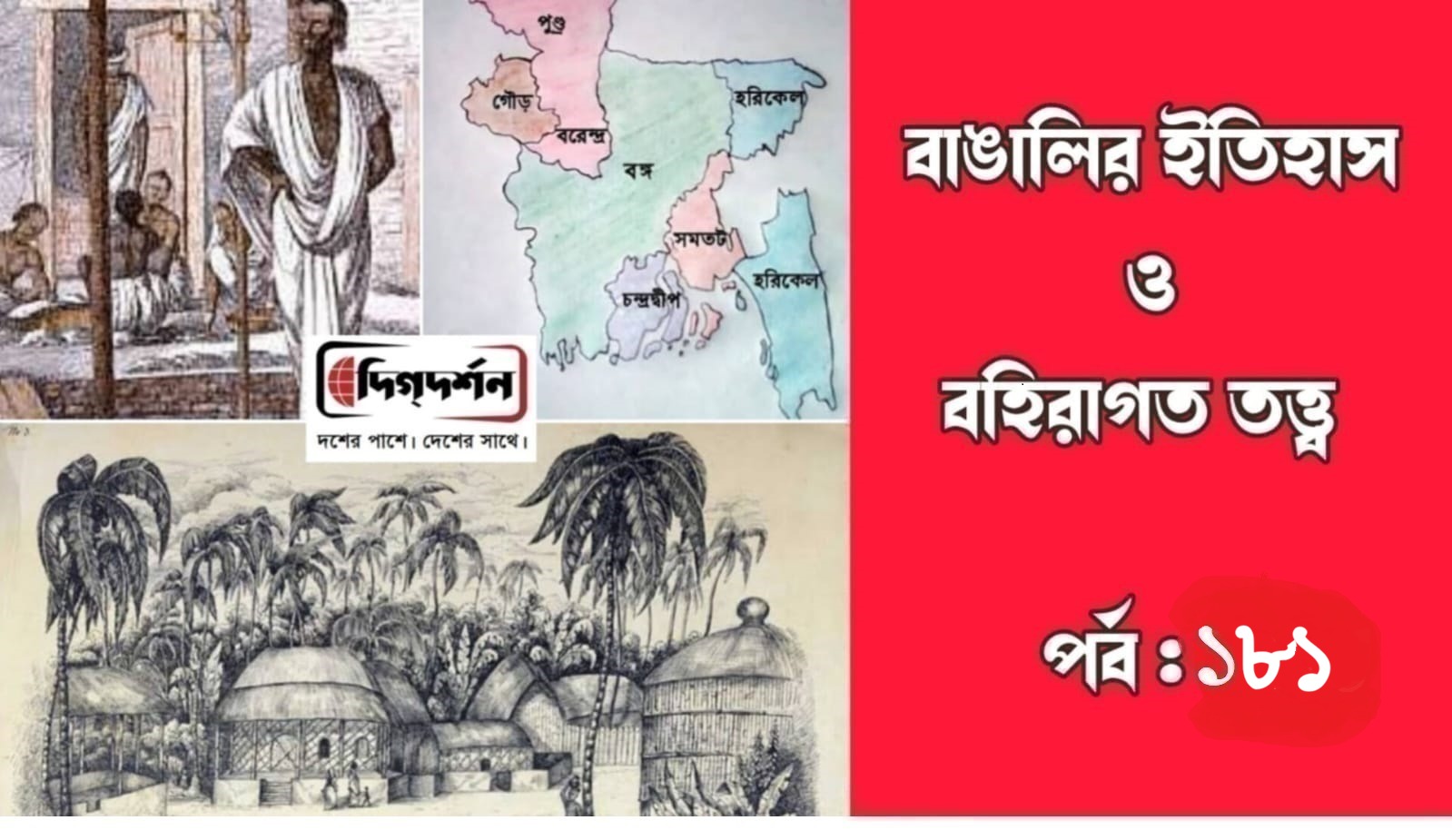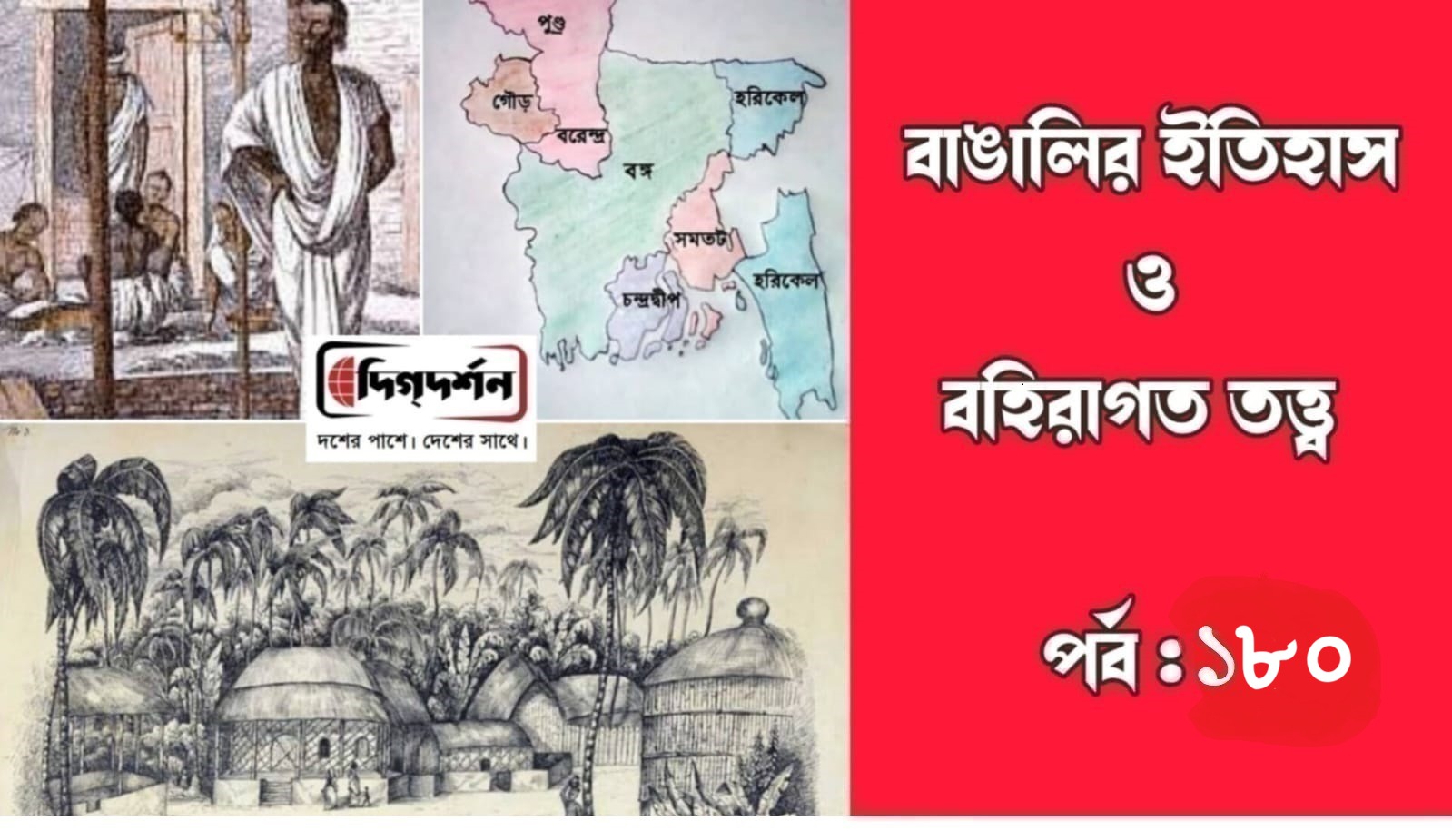করোনা সময়কাল। হঠাৎ একদিন সকালে ভ্রাতৃপ্রতিম সাংবাদিক বন্ধু কুণাল ঘোষের ফোন। কুশল বিনিময়ের পর কুণাল জানালো বাড়িতে যখন বন্দী।, তখন একটা গবেষণামূলক লেখা লিখুন। আমি ই বুকে প্রকাশ করব। বিষয়টি সেই নির্বাচন করে দিল। বাংলা ও বাঙ্গালির ইতিহাস। শুনেই চমকে উঠেছিলাম। কাকে দিচ্ছ রাজার পার্ট। আমি সামান্য এক ক্ষুদ্র সাংবাদিক। এই বিশাল ব্যাপ্তির কাজে হাত দেওয়া মানে সাপের গর্তে হাত ঢোকানো। তবু অনড় কুণাল। ওঁর রাজনৈতিক মতের সঙ্গে আমার হাজার যোজন দূরের সস্পর্ক। কিন্তু কলকাতায় যখন কোনো টিভি চ্যানেলের অস্তিত্ব ছিল না তখন কলকাতা দূরদর্শনে বেসরকারি প্রযোজনায় সংবাদ ম্যাগাজিন তৈরির দুঃসাহস তো দেখিয়েছিলাম কুণালের মত তৎপর সাংবাদিককে পাশে পেয়েছিলাম বলে। বাংলার টেলিভিশন সাংবাদিকতায় যদি পত্তন করতে পারি সাফল্যের সঙ্গে, তবে এই কাজটাও পারব ।। সবচেয়ে বড় কথা,, এই লেখায় আমার কৃতিত্ব নেই। আমার কাজ তো তথ্য সংগ্রহ করে মালা গাঁথা। করোনা প্রবাহে শুরু করেছিলাম। কিন্তু লিখতে গিয়ে দেখলাম বাংলার ঐতিহাসিকদের বহুলাংশই উচ্চবর্ণের মানুষ। ফলে ভূমিপূত্র বাঙ্গালির ইতিহাস, সংস্কৃতি সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। তাই আমার তথ্য খোঁজার কাজটা হলো গোয়েন্দার সূত্র খোঁজার মত।
সেই খুঁজে পাওয়া তথ্য যদি বাঙালির কোনো কাজে লাগে সেই আশায় পর্ব অনুযায়ী পরিবেশন করতে চলেছি। শুধু প্রশংসা নয়,সমালোচনাও চাই। তবে তো নিজের ভুল বা ব্যর্থতা সংশোধন করত পারবো। বিষয়টি যেহেতু কুণাল ঘোষের অনুপ্রেরণায় তাই লেখাটি তাঁকেই উৎসর্গ করছি।
পর্ব:১২৪

৮ ওর ৯ শতাব্দীতে বুদ্ধ ও শিব সর্বশ্রেষ্ঠ উপাস্য ছিল।
সুজিৎ চট্টোপাধ্যায়: আগের পর্বে শিবলিঙ্গের উৎপত্তি তত্ত্ব বলেছি। দীনেশচন্দ্র সেন বৃহৎ বঙ্গ গ্রন্থে লিখেছেন, বুদ্ধ ও শিবের মূর্তি ৮ ম ও ৯ ম শতাব্দীতে সর্বশ্রেষ্ঠ উপাস্য ছিল। এদিকে জায়গা বদলের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় শিব বা বুদ্ধের জায়গা কখনও আর্য দেবতা ব্রহ্মার বা বিষ্ণু দখল করতে পারেনি। বৌদ্ধ ধর্মের পতন এবং বাংলায় হিন্দু ধর্মের শুরুতে প্রথমে আর্য দেবতা বিষ্ণু স্থান পাননি। বুদ্ধ , মহাবীর ও দ্রাবিড় প্রভাব থেকে শিব উপাসক হয় বাঙালির। হিন্দু আগ্রাসনে জাতপাত প্রথাও সেন আমলের শুরু থেকে ঢুকতে শুরু করেছে। সেহিসেবে বাংলার জাতপাতের প্রথার বয়স আটশ বছরের মত। ড: অজিত কুমার সেনগুপ্ত তাঁর ভারত ইতিহাসের বর্ণপ্রথা ( প্রকাশক পাণ্ডুলিপি, কলকাতা ) গ্রন্থের ৮০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন,,,,,,,,, পাল আমলে বর্ণ বিন্যাসের নতুন অধ্যায় সূচিত হয়েছিল। বর্ণ হিসেবে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের পরিচয় এই সময়ে বিশেষ পাওয়া যায় না।

একাদশ শতাব্দীর আগে বাংলায় বিষ্ণুদেব স্বীকৃত ছিলেন না।
তিনি লিখেছেন, অনেকে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকে বাংলার ব্যবসা বাণিজ্যের অবনতির সঙ্গে বৈশ্যদের অনুপস্থিতিকে যুক্ত করেন। পাল রাজা ও রাজন্যবর্গের অনেকে ক্ষত্রিয়ত্ব দাবি করেছেন। তবে সেই দাবি কতটা সংগত তা বলা যায় না। পালরাজারা উচ্চবংশজাত ছিলেন না বলেই মনে হয়। তুলনায় এযুগে করণ কায়স্থদেরঅস্তিত্বের প্রমাণ অনেক বেশি। কবি সন্ধাকর নন্দীর পিতাই ছিলেন করণকূল শ্রেষ্ঠ। তবে ব্রাহ্মণগণও অনেক সময় করণবৃত্তি গ্রহণ করতেন। খ্রিস্টীয় অষ্টম ও দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে ভারতের অন্যত্র বৈদ্য বংশ পৃথক উপবর্ণ গড়ে উঠেছিল।

পাল আমলের শেষ প্রান্তে সেন সাম্রাজ্যের শুরু থেকেই মনুবাদী সংস্কৃতি মেনে চলতে বছর হন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা।
কিন্তু বাংলাদেশে খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্বে বৈদ্য বৃত্তিধারী বৈদ্য উপবর্ণ গঠিত হয়নি। পাল আমলে অনেকসময় রাজ বৈদ্যগণ ‘করণ ‘ বলে তাঁদের পরিচয় দিয়েছেন।,,,,,,, প্রকৃতপক্ষে এযুগে সমাজব্যবস্থায় বৌদ্ধ ব্রাহ্মণে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। সামাজিক ব্যাপারে বৌদ্যগণও মনুর শাসন মেনে চলতেন। ( চলবে)
পরবর্তী পর্ব ১৩ জুলাই,রবিবার,২০২৫